বিশ
শতকের দুই কিংবদন্তি চিন্তাবিদ আর্নল্ড টয়েনবি এবং দাইসাকু ইকেদা। একজন পশ্চিমের ইতিহাসের বাতিঘর, অন্যজন পূর্ব এশিয়ার বৌদ্ধ দর্শনের প্রবক্তা। ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক ভিন্নতা সত্ত্বেও তাঁদের চিন্তা ও দর্শনে এক অভূতপূর্ব মেলবন্ধন লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে সাহিত্য, শিল্প এবং সামাজিক দায়বদ্ধতা নিয়ে তাঁদের ঐতিহাসিক আলাপচারিতা আজও বিশ্বজুড়ে লেখক ও চিন্তাবিদদের নতুন পথের সন্ধান দেয়। সাহিত্যের দায় কি শুধুই ক্ষুধার্ত মানুষের অন্ন জোটানো, নাকি আত্মিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করা? এই গভীর প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে তাঁদের কালজয়ী সিদ্ধান্তের চুলচেরা বিশ্লেষণ নিয়ে আমাদের আজকের এই বিশেষ আয়োজন।
টয়েনবি
ও ইকেদা দুজনেই ছিলেন প্রকৃত জ্ঞানপিপাসু, ইতিহাসসচেতন, মানবতাবাদী এবং বিশ্বমৈত্রীর দূত। নিজেদের লব্ধজ্ঞান ও মনীষার মাধ্যমে তাঁরা জীবনভর মানবিক মূল্যবোধ, অহিংসা, সহনশীলতা ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের উদ্বোধন ঘটিয়ে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় কাজ করে গেছেন। বিগত শতকের শেষার্ধে এই দুই মনীষীর মধ্যকার বৈঠকটি ছিল জ্ঞানতাত্ত্বিক জগতের সবচেয়ে বড় ঘটনা। ১৯৭২ থেকে ১৯৭৩ সালে লন্ডনে টয়েনবির বাসভবনে তাঁদের মধ্যে একাধিক দীর্ঘ বৈঠক ও আলাপচারিতা হয়। এতে মূল আলোচ্য বিষয় ছিল সভ্যতার উত্থান-পতন, বিশ্বযুদ্ধ, শান্তিসংকট, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়ন, মানবতার ভবিষ্যৎ এবং পূর্ব ও পশ্চিমের দর্শনের মেলবন্ধন। ধর্ম, নৈতিকতা, শিক্ষা ও শিল্পের প্রতিটি স্তরে তাঁরা তাঁদের প্রজ্ঞার স্বাক্ষর রেখেছেন।
তখন
পর্যন্ত সারা দুনিয়ায় চলমান ছিল পশ্চিমের একক আধিপত্য। কিন্তু সেই সংলাপে টয়েনবি এক সাহসী ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন। তিনি ইঙ্গিত দেন যে, অচিরেই পূর্ব এশিয়া পশ্চিমের কাছ থেকে বিশ্ব নেতৃত্বের ভার গ্রহণ করবে। টয়েনবি মনে করতেন, পশ্চিমের বস্তুবাদী দর্শনের চেয়ে পূর্বের আধ্যাত্মিক দর্শনের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের শক্তি অনেক বেশি। অন্যদিকে, ইকেদা অত্যন্ত আশাবাদী ছিলেন যে নতুন শতাব্দীতে মানবজাতি রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিকভাবে একীভূত হবে।
ইকেদা ধারণা করতেন, এই পরিবর্তন কোনো বাহ্যিক চাপ বা জোরজবরদস্তি ছাড়াই মানুষের সম্মিলিত উদ্যোগে ও স্বেচ্ছায় আসবে। তবে টয়েনবি কিছুটা বাস্তববাদী ছিলেন; তিনি সতর্ক করেছিলেন যে, এই পরিবর্তনের জন্য মানবজাতিকে হয়তো অত্যন্ত উচ্চ মূল্য দিতে হতে পারে। দুই চিন্তাবিদের এই ভাবনার ফারাক মূলত তাঁদের ভিন্নধর্মী সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল থেকেই উৎসারিত হয়েছিল।
আলাপচারিতায় ইকেদা মানবজীবনে সাহিত্যের প্রভাব নিয়ে ফরাসি দার্শনিক জাঁ পল সার্ত্রের একটি বিখ্যাত জিজ্ঞাসা সামনে আনেন। সার্ত্র প্রশ্ন তুলেছিলেন—ভুখা-নাঙ্গা মানুষের জন্য সাহিত্যের দায় কী? ইকেদা লক্ষ্য করেছেন, সাহিত্যশিল্পে কিছু লেখক সামাজিক দায় স্বীকার করে কাজ করেন, আবার অনেকে শুধুমাত্র শিল্পসৃষ্টিতেই মগ্ন থাকেন। তাঁদের ধারণা, শিল্পসৃষ্টি ছাড়া সাহিত্যের দ্বিতীয় কোনো দায় নেই।
টয়েনবি বিষয়টিকে চমৎকারভাবে বৈজ্ঞানিক গবেষণার সঙ্গে তুলনা করেন। তাঁর মতে, বৈজ্ঞানিক গবেষণা তখনই সফল হয় যখন তা কোনো নির্দিষ্ট উপযোগিতা বা উদ্দেশ্য ছাড়াই নিছক কৌতূহল মেটানোর জন্য করা হয়। বিজ্ঞানের এই আপাতবিরোধী সত্যটি সাহিত্যের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য। তিনি রুশ কথাসাহিত্যিক লিও তলস্তয়ের উদাহরণ টেনে দেখান যে, তলস্তয়ের শিল্পগুণ সমৃদ্ধ প্রথম পর্যায়ের রচনাগুলো (যেমন: ওয়ার অ্যান্ড পিস) সমাজ সংস্কারের উদ্দেশ্যে লেখা দ্বিতীয় পর্যায়ের রচনার চেয়ে অনেক বেশি প্রভাবশালী ও আধিপত্যবিস্তারী ছিল। প্রথম পর্যায়ের রচনার এমন প্রভাবের জন্য টয়েনবি শুধুমাত্র শিল্পগুণকেই কৃতিত্ব দিয়েছেন।
তৎকালীন
সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট সরকারের সাহিত্যিক দর্শনের তীব্র সমালোচনা করেন টয়েনবি। তিনি মনে করতেন, রাজনৈতিক মতাদর্শ যখন সাহিত্যকে নিয়ন্ত্রণ করে, তখন সাহিত্যের শৈল্পিক ও সামাজিক—উভয় দিকই মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কমিউনিস্টরা সাহিত্যকে তাদের সাম্যবাদী আদর্শ ও প্রচারণার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছিল। টয়েনবির পর্যবেক্ষণে, এমন সাহিত্যের ফলাফল হচ্ছে শিল্পসৃষ্টি ও সামাজিক প্রভাবের দারুণ অবনতি।
রুশ ঔপন্যাসিক আলেকজান্ডার সোলঝেনিৎসিনের ওপর চলা রাষ্ট্রীয় নির্যাতনের প্রসঙ্গ টেনে ইকেদাও সহমত পোষণ করেন। তাঁরা দুজনেই মনে করতেন, সরকার বা পার্টির নীতি যখন লেখকের কলম নিয়ন্ত্রণ করে, তখন তা শিল্পী ও সাহিত্যিকদের ওপর সরকারি বলপ্রয়োগের পরাকাষ্ঠা হয়ে দাঁড়ায়। টয়েনবি এখানে স্পষ্ট করেন যে, সামাজিক কল্যাণের নামে সাহিত্যের ওপর যে নিয়ন্ত্রণারোপ করা হয়, তা আদতে সাহিত্যের কণ্ঠরোধ করার নামান্তর।
টয়েনবি
মনে করতেন, মানুষের সৃষ্টিশীল অনুপ্রেরণা আসলে তার আধ্যাত্মিক জগত থেকেই আসে। তিনি ইতালীয় কবি দান্তে আলিগিয়েরির উদাহরণ দিয়ে দেখান যে, দান্তে যখন তাঁর বিখ্যাত 'ডিভাইন কমেডি' রচনা করছিলেন, তখন তাঁর চারপাশের পরিবেশ ছিল অত্যন্ত সংঘাতময় ও খ্রিষ্টবাদী দমনপীড়নের। কিন্তু দান্তে মানসিকভাবে প্রচলিত মতাদর্শের সঙ্গে একাত্ম ছিলেন বলে তিনি আধ্যাত্মিকভাবে স্বাধীন ছিলেন।
টয়েনবির মতে, লেখক বা শিল্পী যতক্ষণ পর্যন্ত বাহ্যিক শৃঙ্খলের ব্যাপারে ভাবিত হন না, ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি আধ্যাত্মিকভাবে মুক্ত। এর বিপরীতে উনিশ শতকের রুশ সাহিত্যের কথা টেনে টয়েনবি বলেন, জারের শাসনে লেখকেরা ভীতসন্ত্রস্ত ছিলেন বলে তখনকার সাহিত্যে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছিল। অর্থাৎ, রাষ্ট্র যখন লেখকদের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি করে, তখন সাহিত্যের স্বাভাবিক বিকাশ রুদ্ধ হয়ে যায়।
লেখকের
মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে খর্ব করার পেছনে টয়েনবি দুটি প্রধান কারণ দেখিয়েছেন—ধর্মীয় বা রাজনৈতিক মতাদর্শকে অন্ধভাবে বাঁচিয়ে রাখা এবং নৈতিকতার খড়্গকে শাণিত রাখা। টয়েনবির দাবি ছিল, সাহিত্যশিল্পে বাধানিষেধ বা সেন্সর সব সময় হিতে বিপরীত কাজ করে। বিশেষ করে ধর্মীয় সেন্সর সাহিত্যের স্বতঃস্ফূর্ততাকে নষ্ট করে দেয়।
ইকেদাও সাহিত্যের এই সেন্সরশিপের বিরুদ্ধে ছিলেন। তবে তিনি সমকালীন সাহিত্যের 'অশ্লীলতা'র প্রবণতা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। ইকেদা মনে করতেন, অশ্লীল সাহিত্যবস্তুর আকর্ষণ ক্ষণস্থায়ী এবং সময়ান্তরে তা উবে যেতে বাধ্য। তবে তরুণ প্রজন্মকে এসবের কুপ্রভাব থেকে দূরে রাখতে হবে। টয়েনবিও একমত ছিলেন যে, কোনো কর্তৃপক্ষের নৈতিক অধিকার নেই অন্য কোনো ধর্ম বা মতাদর্শকে দমন করার। সেন্সরের ভয় শিল্পীর স্বাধীনতা ও সৃজনশীলতাকে সমূলে বিনাশ করে।
নিহিলিস্ট
বা নৈরাশ্যবাদী লেখকদের নিয়ে টয়েনবি ও ইকেদা উভয়েই আলোচনা করেন। তাঁরা মনে করতেন, নিহিলিজম জীবন ও জগতকে অবজ্ঞা করে, যা সমাজে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। ইকেদার মতে, আধুনিক লেখকদের মধ্যে অনেক সময় অন্তর্মুখী হওয়ার প্রবণতা দেখা যায় যা তাঁদের মধ্যে নিহিলিস্ট-সুলভ হতাশার জন্ম দেয়।
টয়েনবি এখানে দুটি বিকল্প পথের সন্ধান পান। প্রথমটি হলো নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নেওয়া এবং দ্বিতীয়টি হলো আধ্যাত্মিক সত্য অনুসন্ধানে একটি সুস্থিতি তৈরি করা। টয়েনবি মনে করতেন, অন্তর্মুখী সাহিত্য নেতিবাচক হবে কি না, তা নির্ভর করে তার স্বরূপের ওপর। যদি তা প্রেরণার উৎস হয়, তবে তাকে স্বাগত জানানো উচিত। তবে নির্দিষ্ট মতবাদ প্রচারকে তিনি সাহিত্যের জন্য দুর্ভাগ্যজনক বলে অভিহিত করেন।
ইকেদা
বিশ্বাস করতেন, সাহিত্যের উদ্দেশ্য আগে থেকে নির্দিষ্ট হওয়া অনুচিত, তবে এর মর্মগত অভিপ্রায় হতে হবে মানুষের জন্য ইতিবাচক প্রেরণা। প্রতিকূল পরিবেশে থেকেও একজন সাহিত্যিককে সাধারণ মানুষের সত্যিকার যন্ত্রণা তুলে ধরতে হবে। তাঁর মতে, সাহিত্য যেন হয় অসহায় মানুষের সুরক্ষার বর্ম। সাহিত্যিককে মহৎ হতে হলে তাঁর স্বাধীনতার মধ্যে মানুষের সত্যিকার হাহাকারকে ধারণ করতে হবে।
অন্যদিকে, টয়েনবি 'বৃত্তিজীবীর শিল্প' বা শুধু বিশেষজ্ঞদের জন্য রচিত সাহিত্যের কড়া সমালোচনা করেন। তিনি একে 'বন্ধ্যা' ও 'ভ্রান্ত শিল্প' বলে অভিহিত করেন। টয়েনবি স্পষ্টভাবে বলেন যে, মুষ্টিমেয়ের জন্য রচিত সাহিত্য, বিজ্ঞান ও শিল্প আদতে সামাজিক রুগ্ণতাকেই প্রকাশ করে। সাহিত্য যদি সর্বজনীন না হয়, তবে তা তার মূল উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত হয়।
টয়েনবি
গ্রিক দার্শনিকদের মতো মনে করতেন, প্রকৃত জ্ঞানলাভের পূর্বশর্ত হচ্ছে যাতনাভোগ। তিনি দান্তের জীবনবোধের মাধ্যমে এটি উপলব্ধি করেছেন। দান্তে প্রেমের যন্ত্রণা ও আবাসস্থল থেকে বিতাড়িত হওয়ার কষ্ট সহ্য করেছিলেন বলেই তাঁর পক্ষে মহৎ কাব্য রচনা সম্ভব হয়েছিল। ইকেদাও মনে করেন, নিজের অটুট বিশ্বাসের কারণেই দান্তে কঠিন পরিস্থিতির মধ্যেও সৃজনশীল থাকতে পেরেছিলেন। ১৯ শতকের অনেক রুশ লেখক সামাজিক উপযোগ সৃষ্টির নামে যে সাহিত্যচর্চা করেছিলেন, তার অসারতা দেখে অনেকে নিহিলিজমের পথে হেঁটেছিলেন, যা ইকেদাকে ব্যথিত করেছিল।
আর্নল্ড
টয়েনবি এবং দাইসাকু ইকেদার এই দীর্ঘ সংলাপ সমাপ্ত হয় এক অসীম আশাবাদের মধ্য দিয়ে। ইকেদা তাঁর চির-আশাবাদী মন নিয়ে এমন এক সাহিত্যের অপেক্ষায় আছেন, যা নিজ সময়ের মানুষের মনে সাহস জোগাবে। তিনি আন্তরিকতা, সহানুভূতি ও সদিচ্ছাপূর্ণ জীবনের অভিব্যক্তির মাধ্যমে মানুষের মর্যাদার অনুসন্ধান করতে চান।
টয়েনবির কণ্ঠেও ছিল মানুষের চূড়ান্ত সফলতার সুর। তিনি বিশ্বাস করতেন, জীবনের সব প্রতিকূলতা আর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করেই মানুষকে এগিয়ে যেতে হবে। এই যাত্রায় সাহিত্য হবে মানুষের সবচেয়ে বড় অস্ত্র—যা সব অশুভ আর নৈরাশ্য কাটিয়ে আমাদের সামনে চলার পথ দেখাবে। মানুষকে তার শেষ লড়াইটা চালিয়ে যেতেই হবে।
পরিশেষে বলা যায়, আর্নল্ড টয়েনবি এবং দাইসাকু ইকেদার এই কালজয়ী সংলাপ কেবল সাহিত্যের ব্যবচ্ছেদ নয়, বরং এটি মানবতার জয়গান। সাহিত্য যখন রাজনৈতিক বা ধর্মীয় শৃঙ্খলমুক্ত হয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে রচিত হয়, তখনই তা প্রকৃত অর্থে মানুষের মুক্তির দিশারি হয়ে ওঠে। সমকালীন পৃথিবীতে লেখক ও শিল্পীদের সামনে সেন্সরশিপ বা মতাদর্শের যে পাহাড়সম চ্যালেঞ্জ রয়েছে, তা মোকাবিলায় এই দুই মনীষীর দর্শন আজও ধ্রুবতারার মতো সত্য। মানুষের জয়গান আর সুন্দরের সাধনাই হোক আগামীর সাহিত্যের মূলমন্ত্র।
এনএম/ধ্রুবকন্ঠ
বিষয় : সাহিত্য বিশ শতক নানা সিদ্ধান্ত
.png)
বৃহস্পতিবার, ০৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
প্রকাশের তারিখ : ০৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
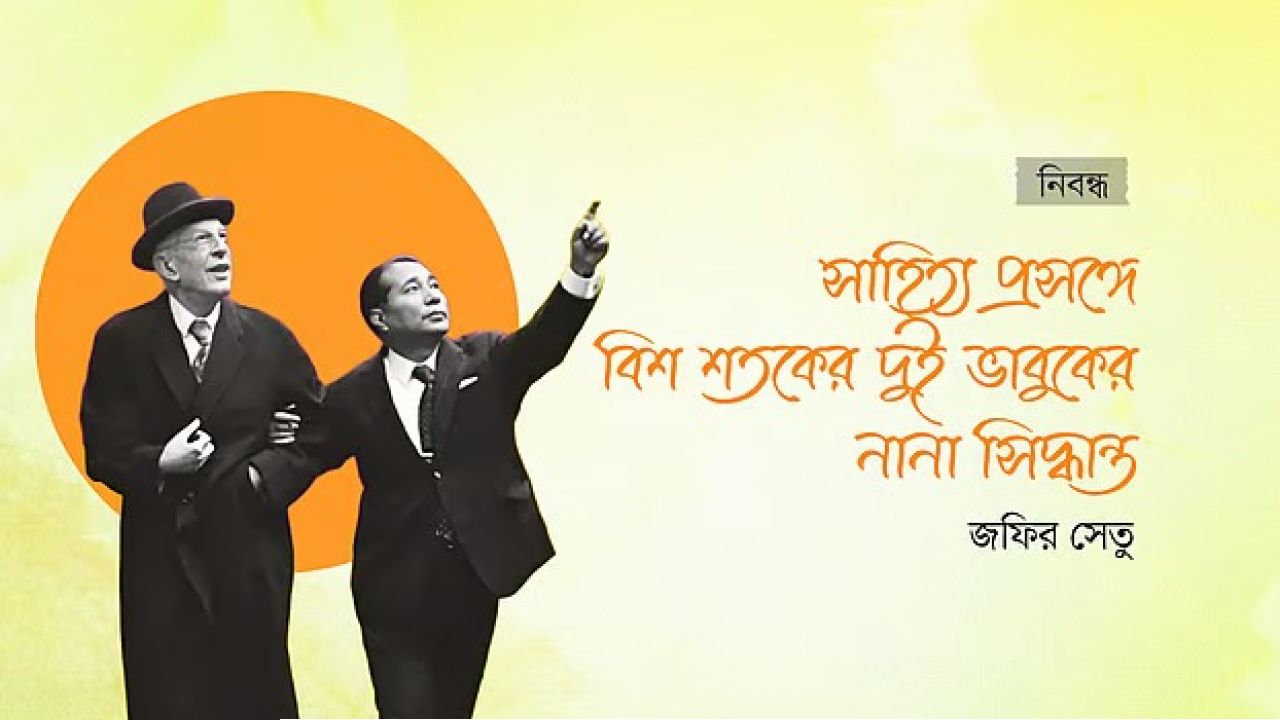
বিশ
শতকের দুই কিংবদন্তি চিন্তাবিদ আর্নল্ড টয়েনবি এবং দাইসাকু ইকেদা। একজন পশ্চিমের ইতিহাসের বাতিঘর, অন্যজন পূর্ব এশিয়ার বৌদ্ধ দর্শনের প্রবক্তা। ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক ভিন্নতা সত্ত্বেও তাঁদের চিন্তা ও দর্শনে এক অভূতপূর্ব মেলবন্ধন লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে সাহিত্য, শিল্প এবং সামাজিক দায়বদ্ধতা নিয়ে তাঁদের ঐতিহাসিক আলাপচারিতা আজও বিশ্বজুড়ে লেখক ও চিন্তাবিদদের নতুন পথের সন্ধান দেয়। সাহিত্যের দায় কি শুধুই ক্ষুধার্ত মানুষের অন্ন জোটানো, নাকি আত্মিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করা? এই গভীর প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে তাঁদের কালজয়ী সিদ্ধান্তের চুলচেরা বিশ্লেষণ নিয়ে আমাদের আজকের এই বিশেষ আয়োজন।
টয়েনবি
ও ইকেদা দুজনেই ছিলেন প্রকৃত জ্ঞানপিপাসু, ইতিহাসসচেতন, মানবতাবাদী এবং বিশ্বমৈত্রীর দূত। নিজেদের লব্ধজ্ঞান ও মনীষার মাধ্যমে তাঁরা জীবনভর মানবিক মূল্যবোধ, অহিংসা, সহনশীলতা ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের উদ্বোধন ঘটিয়ে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় কাজ করে গেছেন। বিগত শতকের শেষার্ধে এই দুই মনীষীর মধ্যকার বৈঠকটি ছিল জ্ঞানতাত্ত্বিক জগতের সবচেয়ে বড় ঘটনা। ১৯৭২ থেকে ১৯৭৩ সালে লন্ডনে টয়েনবির বাসভবনে তাঁদের মধ্যে একাধিক দীর্ঘ বৈঠক ও আলাপচারিতা হয়। এতে মূল আলোচ্য বিষয় ছিল সভ্যতার উত্থান-পতন, বিশ্বযুদ্ধ, শান্তিসংকট, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়ন, মানবতার ভবিষ্যৎ এবং পূর্ব ও পশ্চিমের দর্শনের মেলবন্ধন। ধর্ম, নৈতিকতা, শিক্ষা ও শিল্পের প্রতিটি স্তরে তাঁরা তাঁদের প্রজ্ঞার স্বাক্ষর রেখেছেন।
তখন
পর্যন্ত সারা দুনিয়ায় চলমান ছিল পশ্চিমের একক আধিপত্য। কিন্তু সেই সংলাপে টয়েনবি এক সাহসী ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন। তিনি ইঙ্গিত দেন যে, অচিরেই পূর্ব এশিয়া পশ্চিমের কাছ থেকে বিশ্ব নেতৃত্বের ভার গ্রহণ করবে। টয়েনবি মনে করতেন, পশ্চিমের বস্তুবাদী দর্শনের চেয়ে পূর্বের আধ্যাত্মিক দর্শনের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের শক্তি অনেক বেশি। অন্যদিকে, ইকেদা অত্যন্ত আশাবাদী ছিলেন যে নতুন শতাব্দীতে মানবজাতি রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিকভাবে একীভূত হবে।
ইকেদা ধারণা করতেন, এই পরিবর্তন কোনো বাহ্যিক চাপ বা জোরজবরদস্তি ছাড়াই মানুষের সম্মিলিত উদ্যোগে ও স্বেচ্ছায় আসবে। তবে টয়েনবি কিছুটা বাস্তববাদী ছিলেন; তিনি সতর্ক করেছিলেন যে, এই পরিবর্তনের জন্য মানবজাতিকে হয়তো অত্যন্ত উচ্চ মূল্য দিতে হতে পারে। দুই চিন্তাবিদের এই ভাবনার ফারাক মূলত তাঁদের ভিন্নধর্মী সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল থেকেই উৎসারিত হয়েছিল।
আলাপচারিতায় ইকেদা মানবজীবনে সাহিত্যের প্রভাব নিয়ে ফরাসি দার্শনিক জাঁ পল সার্ত্রের একটি বিখ্যাত জিজ্ঞাসা সামনে আনেন। সার্ত্র প্রশ্ন তুলেছিলেন—ভুখা-নাঙ্গা মানুষের জন্য সাহিত্যের দায় কী? ইকেদা লক্ষ্য করেছেন, সাহিত্যশিল্পে কিছু লেখক সামাজিক দায় স্বীকার করে কাজ করেন, আবার অনেকে শুধুমাত্র শিল্পসৃষ্টিতেই মগ্ন থাকেন। তাঁদের ধারণা, শিল্পসৃষ্টি ছাড়া সাহিত্যের দ্বিতীয় কোনো দায় নেই।
টয়েনবি বিষয়টিকে চমৎকারভাবে বৈজ্ঞানিক গবেষণার সঙ্গে তুলনা করেন। তাঁর মতে, বৈজ্ঞানিক গবেষণা তখনই সফল হয় যখন তা কোনো নির্দিষ্ট উপযোগিতা বা উদ্দেশ্য ছাড়াই নিছক কৌতূহল মেটানোর জন্য করা হয়। বিজ্ঞানের এই আপাতবিরোধী সত্যটি সাহিত্যের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য। তিনি রুশ কথাসাহিত্যিক লিও তলস্তয়ের উদাহরণ টেনে দেখান যে, তলস্তয়ের শিল্পগুণ সমৃদ্ধ প্রথম পর্যায়ের রচনাগুলো (যেমন: ওয়ার অ্যান্ড পিস) সমাজ সংস্কারের উদ্দেশ্যে লেখা দ্বিতীয় পর্যায়ের রচনার চেয়ে অনেক বেশি প্রভাবশালী ও আধিপত্যবিস্তারী ছিল। প্রথম পর্যায়ের রচনার এমন প্রভাবের জন্য টয়েনবি শুধুমাত্র শিল্পগুণকেই কৃতিত্ব দিয়েছেন।
তৎকালীন
সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট সরকারের সাহিত্যিক দর্শনের তীব্র সমালোচনা করেন টয়েনবি। তিনি মনে করতেন, রাজনৈতিক মতাদর্শ যখন সাহিত্যকে নিয়ন্ত্রণ করে, তখন সাহিত্যের শৈল্পিক ও সামাজিক—উভয় দিকই মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কমিউনিস্টরা সাহিত্যকে তাদের সাম্যবাদী আদর্শ ও প্রচারণার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছিল। টয়েনবির পর্যবেক্ষণে, এমন সাহিত্যের ফলাফল হচ্ছে শিল্পসৃষ্টি ও সামাজিক প্রভাবের দারুণ অবনতি।
রুশ ঔপন্যাসিক আলেকজান্ডার সোলঝেনিৎসিনের ওপর চলা রাষ্ট্রীয় নির্যাতনের প্রসঙ্গ টেনে ইকেদাও সহমত পোষণ করেন। তাঁরা দুজনেই মনে করতেন, সরকার বা পার্টির নীতি যখন লেখকের কলম নিয়ন্ত্রণ করে, তখন তা শিল্পী ও সাহিত্যিকদের ওপর সরকারি বলপ্রয়োগের পরাকাষ্ঠা হয়ে দাঁড়ায়। টয়েনবি এখানে স্পষ্ট করেন যে, সামাজিক কল্যাণের নামে সাহিত্যের ওপর যে নিয়ন্ত্রণারোপ করা হয়, তা আদতে সাহিত্যের কণ্ঠরোধ করার নামান্তর।
টয়েনবি
মনে করতেন, মানুষের সৃষ্টিশীল অনুপ্রেরণা আসলে তার আধ্যাত্মিক জগত থেকেই আসে। তিনি ইতালীয় কবি দান্তে আলিগিয়েরির উদাহরণ দিয়ে দেখান যে, দান্তে যখন তাঁর বিখ্যাত 'ডিভাইন কমেডি' রচনা করছিলেন, তখন তাঁর চারপাশের পরিবেশ ছিল অত্যন্ত সংঘাতময় ও খ্রিষ্টবাদী দমনপীড়নের। কিন্তু দান্তে মানসিকভাবে প্রচলিত মতাদর্শের সঙ্গে একাত্ম ছিলেন বলে তিনি আধ্যাত্মিকভাবে স্বাধীন ছিলেন।
টয়েনবির মতে, লেখক বা শিল্পী যতক্ষণ পর্যন্ত বাহ্যিক শৃঙ্খলের ব্যাপারে ভাবিত হন না, ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি আধ্যাত্মিকভাবে মুক্ত। এর বিপরীতে উনিশ শতকের রুশ সাহিত্যের কথা টেনে টয়েনবি বলেন, জারের শাসনে লেখকেরা ভীতসন্ত্রস্ত ছিলেন বলে তখনকার সাহিত্যে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছিল। অর্থাৎ, রাষ্ট্র যখন লেখকদের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি করে, তখন সাহিত্যের স্বাভাবিক বিকাশ রুদ্ধ হয়ে যায়।
লেখকের
মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে খর্ব করার পেছনে টয়েনবি দুটি প্রধান কারণ দেখিয়েছেন—ধর্মীয় বা রাজনৈতিক মতাদর্শকে অন্ধভাবে বাঁচিয়ে রাখা এবং নৈতিকতার খড়্গকে শাণিত রাখা। টয়েনবির দাবি ছিল, সাহিত্যশিল্পে বাধানিষেধ বা সেন্সর সব সময় হিতে বিপরীত কাজ করে। বিশেষ করে ধর্মীয় সেন্সর সাহিত্যের স্বতঃস্ফূর্ততাকে নষ্ট করে দেয়।
ইকেদাও সাহিত্যের এই সেন্সরশিপের বিরুদ্ধে ছিলেন। তবে তিনি সমকালীন সাহিত্যের 'অশ্লীলতা'র প্রবণতা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। ইকেদা মনে করতেন, অশ্লীল সাহিত্যবস্তুর আকর্ষণ ক্ষণস্থায়ী এবং সময়ান্তরে তা উবে যেতে বাধ্য। তবে তরুণ প্রজন্মকে এসবের কুপ্রভাব থেকে দূরে রাখতে হবে। টয়েনবিও একমত ছিলেন যে, কোনো কর্তৃপক্ষের নৈতিক অধিকার নেই অন্য কোনো ধর্ম বা মতাদর্শকে দমন করার। সেন্সরের ভয় শিল্পীর স্বাধীনতা ও সৃজনশীলতাকে সমূলে বিনাশ করে।
নিহিলিস্ট
বা নৈরাশ্যবাদী লেখকদের নিয়ে টয়েনবি ও ইকেদা উভয়েই আলোচনা করেন। তাঁরা মনে করতেন, নিহিলিজম জীবন ও জগতকে অবজ্ঞা করে, যা সমাজে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। ইকেদার মতে, আধুনিক লেখকদের মধ্যে অনেক সময় অন্তর্মুখী হওয়ার প্রবণতা দেখা যায় যা তাঁদের মধ্যে নিহিলিস্ট-সুলভ হতাশার জন্ম দেয়।
টয়েনবি এখানে দুটি বিকল্প পথের সন্ধান পান। প্রথমটি হলো নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নেওয়া এবং দ্বিতীয়টি হলো আধ্যাত্মিক সত্য অনুসন্ধানে একটি সুস্থিতি তৈরি করা। টয়েনবি মনে করতেন, অন্তর্মুখী সাহিত্য নেতিবাচক হবে কি না, তা নির্ভর করে তার স্বরূপের ওপর। যদি তা প্রেরণার উৎস হয়, তবে তাকে স্বাগত জানানো উচিত। তবে নির্দিষ্ট মতবাদ প্রচারকে তিনি সাহিত্যের জন্য দুর্ভাগ্যজনক বলে অভিহিত করেন।
ইকেদা
বিশ্বাস করতেন, সাহিত্যের উদ্দেশ্য আগে থেকে নির্দিষ্ট হওয়া অনুচিত, তবে এর মর্মগত অভিপ্রায় হতে হবে মানুষের জন্য ইতিবাচক প্রেরণা। প্রতিকূল পরিবেশে থেকেও একজন সাহিত্যিককে সাধারণ মানুষের সত্যিকার যন্ত্রণা তুলে ধরতে হবে। তাঁর মতে, সাহিত্য যেন হয় অসহায় মানুষের সুরক্ষার বর্ম। সাহিত্যিককে মহৎ হতে হলে তাঁর স্বাধীনতার মধ্যে মানুষের সত্যিকার হাহাকারকে ধারণ করতে হবে।
অন্যদিকে, টয়েনবি 'বৃত্তিজীবীর শিল্প' বা শুধু বিশেষজ্ঞদের জন্য রচিত সাহিত্যের কড়া সমালোচনা করেন। তিনি একে 'বন্ধ্যা' ও 'ভ্রান্ত শিল্প' বলে অভিহিত করেন। টয়েনবি স্পষ্টভাবে বলেন যে, মুষ্টিমেয়ের জন্য রচিত সাহিত্য, বিজ্ঞান ও শিল্প আদতে সামাজিক রুগ্ণতাকেই প্রকাশ করে। সাহিত্য যদি সর্বজনীন না হয়, তবে তা তার মূল উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত হয়।
টয়েনবি
গ্রিক দার্শনিকদের মতো মনে করতেন, প্রকৃত জ্ঞানলাভের পূর্বশর্ত হচ্ছে যাতনাভোগ। তিনি দান্তের জীবনবোধের মাধ্যমে এটি উপলব্ধি করেছেন। দান্তে প্রেমের যন্ত্রণা ও আবাসস্থল থেকে বিতাড়িত হওয়ার কষ্ট সহ্য করেছিলেন বলেই তাঁর পক্ষে মহৎ কাব্য রচনা সম্ভব হয়েছিল। ইকেদাও মনে করেন, নিজের অটুট বিশ্বাসের কারণেই দান্তে কঠিন পরিস্থিতির মধ্যেও সৃজনশীল থাকতে পেরেছিলেন। ১৯ শতকের অনেক রুশ লেখক সামাজিক উপযোগ সৃষ্টির নামে যে সাহিত্যচর্চা করেছিলেন, তার অসারতা দেখে অনেকে নিহিলিজমের পথে হেঁটেছিলেন, যা ইকেদাকে ব্যথিত করেছিল।
আর্নল্ড
টয়েনবি এবং দাইসাকু ইকেদার এই দীর্ঘ সংলাপ সমাপ্ত হয় এক অসীম আশাবাদের মধ্য দিয়ে। ইকেদা তাঁর চির-আশাবাদী মন নিয়ে এমন এক সাহিত্যের অপেক্ষায় আছেন, যা নিজ সময়ের মানুষের মনে সাহস জোগাবে। তিনি আন্তরিকতা, সহানুভূতি ও সদিচ্ছাপূর্ণ জীবনের অভিব্যক্তির মাধ্যমে মানুষের মর্যাদার অনুসন্ধান করতে চান।
টয়েনবির কণ্ঠেও ছিল মানুষের চূড়ান্ত সফলতার সুর। তিনি বিশ্বাস করতেন, জীবনের সব প্রতিকূলতা আর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করেই মানুষকে এগিয়ে যেতে হবে। এই যাত্রায় সাহিত্য হবে মানুষের সবচেয়ে বড় অস্ত্র—যা সব অশুভ আর নৈরাশ্য কাটিয়ে আমাদের সামনে চলার পথ দেখাবে। মানুষকে তার শেষ লড়াইটা চালিয়ে যেতেই হবে।
পরিশেষে বলা যায়, আর্নল্ড টয়েনবি এবং দাইসাকু ইকেদার এই কালজয়ী সংলাপ কেবল সাহিত্যের ব্যবচ্ছেদ নয়, বরং এটি মানবতার জয়গান। সাহিত্য যখন রাজনৈতিক বা ধর্মীয় শৃঙ্খলমুক্ত হয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে রচিত হয়, তখনই তা প্রকৃত অর্থে মানুষের মুক্তির দিশারি হয়ে ওঠে। সমকালীন পৃথিবীতে লেখক ও শিল্পীদের সামনে সেন্সরশিপ বা মতাদর্শের যে পাহাড়সম চ্যালেঞ্জ রয়েছে, তা মোকাবিলায় এই দুই মনীষীর দর্শন আজও ধ্রুবতারার মতো সত্য। মানুষের জয়গান আর সুন্দরের সাধনাই হোক আগামীর সাহিত্যের মূলমন্ত্র।
এনএম/ধ্রুবকন্ঠ
.png)
আপনার মতামত লিখুন